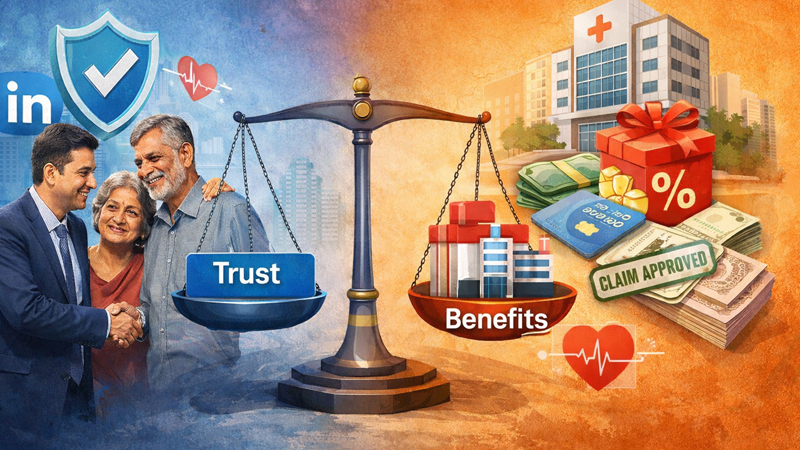বীমা খাতে আস্থা ফেরাতে মৌলিক নীতিগুলোই হতে পারে শেষ ভরসা
.jpg)
রাজ কিরণ দাস: জীবন, স্বাস্থ্য, ব্যবসা, বাড়ি- সবকিছুর মধ্যেই এখন ঝুঁকি যেন অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী। হঠাৎ অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা বাজারের অস্থিরতা- প্রতিটি অনিশ্চয়তার মাঝে মানুষ যে ক’টি প্রতিষ্ঠানের ওপর ভরসা রাখতে চায়, তার মধ্যে বীমা প্রতিষ্ঠান অন্যতম। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই ভরসার ভিতটা দাঁড়িয়ে আছে কোথায়?
বীমা শুধু একটি আর্থিক চুক্তি নয়; এটি আস্থার বিনিময়, নৈতিকতার পরীক্ষা এবং দায়িত্ববোধের বাস্তব প্রয়োগ। আর এই পুরো কাঠামোকে সুসংহত রাখতে যে মৌলিক নীতিগুলো কাজ করে, সেগুলোকে নিছক পাঠ্যবইয়ের তত্ত্ব ভেবে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই। বরং বলা যায়, এগুলোই বীমা খাতের অঘোষিত পরিচালনপত্র।
বীমা ব্যবসা মূলত বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে। গ্রাহক প্রিমিয়াম পরিশোধ করেন ভবিষ্যতের কোনো অনিশ্চিত ঘটনার আশঙ্কায়, আর প্রতিষ্ঠান প্রতিশ্রুতি দেয় সেই আশঙ্কা সত্যি হলে আর্থিক সুরক্ষা দেয়ার। এখানে দু’পক্ষেরই দায়িত্ব রয়েছে- গ্রাহকের দায়িত্ব পুরো সত্যটি জানানো, প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ন্যায়সংগত শর্তে সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
এই জায়গাতেই উত্তম বিশ্বাসের নীতি সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। যখন গ্রাহক সঠিক তথ্য দেন না, অথবা প্রতিষ্ঠান ইচ্ছে করে অস্পষ্ট শর্ত রেখে চুক্তি করে, তখন শুধু একটা পলিসি নয়- পুরো খাতের ওপরই সাধারণ মানুষের আস্থা নড়ে যায়। আর একবার সেই আস্থা ভাঙলে তা পুনর্গঠন করা সহজ নয়।
বীমা চুক্তিতে প্রকৃত আর্থিক স্বার্থ থাকা বাধ্যতামূলক- এই নীতি শুধু আইনগত নয়, নৈতিক দৃষ্টিতেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তখনই কোনো সম্পদ বা জীবনের ওপর বীমা করতে পারে, যখন সেই ঝুঁকি বাস্তবে তাদের জন্য আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে।
এর ফলে বীমা শিল্পকে সম্ভাব্য অপব্যবহার থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। যদি যার কোনো ক্ষতি হবে না, সে-ও বীমা করার সুযোগ পেত, তবে উদ্দেশ্য হয়ে যেত লাভ করার প্রবণতা, সুরক্ষা নয়। এটি বীমাকে ঝুঁকিপূর্ণ জুয়া বা বাজির মতো করে তুলত, যা শেষ পর্যন্ত সমাজ ও অর্থনীতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতো।
কোনো দুর্ঘটনা বা ঘটনার ফলে যে ক্ষতি হলো, তার সঙ্গে বীমাকৃত ঝুঁকির সরাসরি ও যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক থাকতে হবে- এটি বীমা দাবি নিষ্পত্তির মূল ভিত্তি। যদি ক্ষতির পেছনে এমন কোনো কারণ কাজ করে, যা বীমার আওতায় নয়, তবে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে: প্রতিষ্ঠান কতদূর পর্যন্ত দায় নেবে?
এই প্রশ্নের ন্যায়সঙ্গত উত্তর আসে কারণ-সম্পর্কের সঠিক বিশ্লেষণ থেকে। এতে গ্রাহকও জানেন, কোন ধরনের ঝুঁকি কাভার হচ্ছে আর কোনটি হচ্ছে না; প্রতিষ্ঠানও জানে, কী পরিমাণ দায় তাদের বহন করতে হবে। স্বচ্ছতা ও পূর্বানুমেয়তার এই সমন্বয়ই বীমার প্রতি আস্থা বাড়ায়।
বীমা ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্য লাভ করিয়ে দেয়া নয়, বরং যে ক্ষতি হয়েছে তা থেকে গ্রাহককে পুনরুদ্ধার করা- এই নীতিই বীমার নৈতিক ভিত্তি শক্ত করে। গ্রাহক যদি বীমা দাবি থেকে লাভবান হতে পারেন, তবে কোথাও গিয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে দুর্ঘটনা ঘটানোর বা অতিরঞ্জিত দাবি তোলার প্রবণতা তৈরি হতে পারে।
অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠান যদি প্রকৃত ক্ষতির কম টাকা পরিশোধ করে, তবে সেটাও ন্যায়বিচারবহির্ভূত আচরণ। সুতরাং, ন্যায্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণই বীমা চুক্তিকে দু’পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য রাখে এবং বাজারকে স্থিতিশীল করে।
অনেক সময়ই ঘটে, যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ক্ষতির শিকার হয়েছে, তার আসল ক্ষতির কারণ আরেকজন। ধরুন, কোনো চালকের অবহেলায় দুর্ঘটনা ঘটল, আর গাড়ির মালিক বীমা দাবি করলেন। বীমা প্রতিষ্ঠান গ্রাহককে ক্ষতিপূরণ দিলেও, প্রকৃত দায় কিন্তু সেই অবহেলাকারী চালকের।
এমন পরিস্থিতিতে তৃতীয় পক্ষের দায় নির্ধারণের সুযোগ থাকা বীমা ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে গ্রাহক দ্রুত ক্ষতিপূরণ পেলেও, শেষ পর্যন্ত আর্থিক দায় যেখানে থাকা উচিত সেখানে স্থানান্তরিত হয়। একইভাবে, একাধিক বীমা থাকলে, দায় নিরপেক্ষভাবে সবার মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। এর ফলে কোনো প্রতিষ্ঠান একা অতিরিক্ত চাপ বহন করতে হয় না, আর কেউ আবার একই ক্ষতির জন্য একাধিক দাবির মাধ্যমে বেআইনি সুবিধাও নিতে পারে না।
বীমা থাকা মানে এই নয় যে গ্রাহক নির্ভার হয়ে যাবেন। বরং ক্ষতি শুরু হওয়ার পর তা কমিয়ে আনার জন্য দ্রুত ও যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নেয়া গ্রাহকেরই দায়িত্ব। বাড়িতে আগুন লাগলে নেভানোর চেষ্টা না করে শুধু ভিডিও করে রাখা যেমন দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ, তেমনি দুর্ঘটনার পর প্রমাণ নষ্ট করাও অসৎ উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত দেয়।
বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো তাই যুক্তি দেয়, তারা অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষতির আর্থিক বোঝা ভাগ করতে প্রস্তুত, কিন্তু অবহেলা বা ইচ্ছাকৃত ক্ষতির দায় নিতে প্রস্তুত নয়। এই নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বীমাকে কেবল অর্থনৈতিক নয়, সামাজিকভাবেও দায়িত্বশীল একটি ব্যবস্থায় পরিণত করে।
বিশ্ব এখন দ্রুত ডিজিটাল হচ্ছে। অনলাইন পলিসি, মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে দাবি, স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি বিশ্লেষণ- সবকিছু বদলে যাচ্ছে। তবে মৌলিক নীতিগুলো না বুঝে যদি শুধু প্রযুক্তিনির্ভর বীমা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়, তাহলে তা হবে অনিশ্চিত ভিত্তির ওপর কাঁচের অট্টালিকা দাঁড় করানোর মতো।
বীমা প্রতারণা, অতিরিক্ত দাবির প্রবণতা, অস্পষ্ট শর্ত, গ্রাহকের অজ্ঞতা- এসব সমস্যা এখনো বাস্তব। এর মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন, মহামারি, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার মতো নতুন ঝুঁকিও যুক্ত হয়েছে। এই সবকিছুর সমন্বিত সমাধানে বীমার নীতিগুলোকে কেবল আইনগত পাঠ্য নয়, কার্যকর নীতি-দর্শন হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।
একদিকে গ্রাহককে সচেতন হতে হবে, তিনি কীসের জন্য প্রিমিয়াম দিচ্ছেন, কী শর্তে দাবি করতে পারবেন, আর তার নিজের দায়িত্ব কী। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিত করতে হবে, নীতিগুলোর বিরোধী কোনো চর্চা যেন ব্যবসার স্বল্পমেয়াদি লাভের জন্য উৎসাহিত না হয়। নীতি-ভিত্তিক স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচার ছাড়া টেকসই বীমা শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব নয়।